খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের সূচনায় বাঙালি কবি কাশীরাম দাস বেদব্যাস কৃত সংস্কৃত ভাষার মহাভারতকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করলেও কাব্য সৃষ্টির অনিবার্য নিয়মে তাঁর কাব্যে বাংলার এবং সমসাময়িক কালের প্রতিফলন ঘটেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার সামাজিক ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এসময়কার বাংলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যজীবনের এবং বৈষ্ণবধর্মের পরিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। যদিও গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এযুগের সমগ্র বাঙালি সমাজ বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ করে নেয়নি ঠিকই, কিন্তু তবুও মহাপ্রভুর দিব্যজীবন এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় ও জীবন চেতনায় এযুগের সমস্ত বাঙালিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এবিষয়গুলি তখনকার বাঙালির জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেকালের বাংলার হিন্দুদের জীবন অনেকাংশে ভগবৎ নির্ভর ছিল বলে ভগবৎচেতনা, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের কাছে মানুষের কামনা—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই বাঙালি হিন্দুদের জীবনযাত্রা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হত। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে বাঙালি হিন্দুরা কিন্তু পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্যরূপের সাধনা করতেন। এসময়ে তাঁরা বিভিন্ন আচার বিচারের মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে নিজেদের সহস্র কামনা জ্ঞাপন করেছিলেন। বস্তুতঃ সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে যেসব লৌকিক দেবতা বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদেরও শক্তিরূপের কাছে হিন্দু বাঙালিরা অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার, এবং বিভিন্ন পার্থিব সুখ সম্পদের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।
এরপরে মহাপ্রভু এসে দেবতার কাছে নিত্য কামনার এই মানসিক দৈন্য থেকে বাঙালি হিন্দুকে মুক্ত করে রাগানুগাভক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন। আর অতীত থেকেই বাঙালি হিন্দুরা যেহেতু স্বভাবগতভাবে ভাবপ্রবণ ছিলেন, সেহেতু জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম, এবং ভগবৎ সাধনা—এই ত্রিবিধ পথের মধ্যে তাঁরা তখন প্রেমের সহজ ও প্রশস্ত পথকেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। একইসাথে মহাপ্রভুর আবেগ প্রধান ভগবৎ সাধনাও সহজেই তখন সমস্ত বাঙালি চিত্তকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিল। বস্তুতঃ হৃদয় ধর্মপ্রধান প্রেমসাধনার ক্ষেত্রে তিনি বাঙালিকে একটি নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখন একথা আর নতুন করে বলবার নয় যে, মহাপ্রভু নিজেই বিরহবিপ্রলম্ভের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভালবাসা ছিল জন্ম জন্মান্তরের; আর একারণেই তিনি বহিরঙ্গে রাধা ও অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ-রাধা ভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ ছিলেন। তাই যে প্রেম সাধনায় তিনি নিজে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সেটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হলেও, সর্বসাধারণের জন্য কিন্তু আয়ত্তের অতীত ছিল। সাধারণভাবে বৈষ্ণব দর্শন বলে যে, জীব সাধারণের জন্য রাগানুগাভক্তিই প্রশস্ত। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি বা মমত্ববুদ্ধি না থাকলে কারো পক্ষেই এই রাগানুগাভক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।
বৈষ্ণবধর্মানুসারে এই আসক্তি বা রতি হল পাঁচ প্রকারের; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আলোচ্য সময়ে এই পাঁচটি রতিতেই ভগবদ্ভক্ত বাঙালি হিন্দুরা ঈশ্বরচিন্তাকে নিজের প্রাণের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলেন। এরফলে তাঁদের ঈশ্বরচিন্তা একটি নতুন পথ পরিগ্রহ করেছিল; এর আগে প্রচলিত থাকা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বা শক্তিরূপের পরিবর্তে এসময়কার বাঙালি হিন্দুরা তাঁকে প্রধানতঃ আনন্দরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, এবং এরফলে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের আগেকার ব্যবধান হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এর আগে ভক্তের সাথে ঈশ্বরের শুধুই ভক্তির সম্বন্ধ ছিল, আর ক্রমে এই ভক্তির সঙ্গে ভীতিও যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর কাল থেকে ঈশ্বরে ভক্তির সঙ্গে ভক্তের প্রীতি মিশ্রিত হয়েছিল, আর ঈশ্বরের কাছে ঐহিক সুখ-সম্পদ, অথবা পারমার্থিক মুক্তির পরিবর্তে ভালোবাসাই ভক্তের কাম্য হয়ে উঠেছিল। এমনকি তখন যাঁরা বৈষ্ণবধর্মকে গোষ্ঠীগত সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নি, তাঁরাও এই নতুন বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এভাবেই মধ্যযুগের বাংলায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাঙালি হিন্দুদের জীবন কৃষ্ণ-ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং পার্থিব সুখ লাভের পরিবর্তে শুদ্ধাভক্তিই তাঁদের কাছে একমাত্র কাম্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলায় এই ভাবধারায় পরিবর্ধিত হয়ে উঠেই কবি কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারত কাব্যটি রচনা করেছিলেন।
তখনকার এই যুগপ্রভাবের ফলে কৃষ্ণ-ভক্তিতে তাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ ছিল, এবং এই মানসিক অবস্থাতেই তিনি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের মূল কাহিনীতে কৃষ্ণের যে ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়, সেটা তাঁর চিত্তের মধ্যে ভক্তির সুগভীর রাগিণীর সৃষ্টি করেছিল। আর এটাই তখন তাঁকে মহাভারত কাহিনীর আধারে মধ্যযুগের বাঙালির সামনে কৃষ্ণকথা পরিবেশন করবার একটা অবকাশ করে দিয়েছিল। এরপরে একারণেই এই বাঙালি কবি যখন তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেছিলেন, তখন দেখা গিয়েছিল যে, এতে মূল মহাভারত গ্রন্থের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ব্যাসদেব রচিত সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মহাভারতের কাহিনীর সাথে যাঁরা অবগত রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, এতে পরস্পর আত্মীয় রাজন্যদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে, এবং এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের উত্থান পতনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সেযুগের ভারতে রাজশক্তির এই পতন অভ্যুদয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে একইসাথে তিনি এই বিবাদমান রাজন্যদের আত্মীয় ও বন্ধু, এবং সেকালের অন্যতম প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারতে তাঁর মধ্যে থাকা মানবিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি আবার তাঁর ভগবৎ পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের এই পরিচয় কখনোই তাঁর প্রধান বা একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে কাশী দাসের রচনায় কিন্তু কৃষ্ণের মানবিক কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং এতে ভগবৎ পরিচয়ই তাঁর একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়, এবং এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর ভগবৎসত্তা নিয়েই সমস্ত কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এরফলে কাশীদাসী মহাভারতে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবর্তে, প্রবলের অত্যাচার থেকে ঈশ্বর কিভাবে নিজের ভক্তকে উদ্ধার করেছিলেন, এটাই প্রকাশিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। এতে দুর্যোধন হলেন শক্তিমান, অহংকারী ও অত্যাচারী। আর নিজেদের এই জ্ঞাতি শত্রুর হাতে পাণ্ডুপুত্ররা অসহায়ভাবে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেছেন; তাঁরা পিতৃহীন অনাথ, তাঁদের সহায় সম্বল বলে কিছুই নেই, শুধুমাত্র দীন দরিদ্রের একমাত্র সম্বল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অবিচল ভক্তি আর ভালোবাসা রয়েছে। একারণেই কাশীরাম দাসের সৃষ্ট যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা প্রায়শঃই শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের অসহায় বেদনা নিবেদন করে বলেছিলেন—
“বিস্তর করিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ॥
না জানি পূর্বেতে কত করিনু কুকর্ম।
সে কারণে দুঃখ শোকে গেল মম জন্ম॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে পিতা মম গেলা পরলোক॥
পোঁহাইনু সেই কাল পরের আলয়ে।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে॥
তারপর দুষ্টুবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ এমন সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এসব সঙ্কট হইতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমত সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥”
কাশীরাম দাসের রচনায় ভক্তের প্রেমডোরে বাঁধা ঈশ্বর নিজের মাহাত্ম্যে অসহায় পাণ্ডুপুত্রদের উদ্ধার করেছিলেন। মধুযুগের বাংলার কবির হাত দিয়ে মূল মহাভারতের কাহিনীর এই প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেশ ও কালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবকেই নির্দেশ করে।
এতে যে কৃষ্ণকথা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কৃষ্ণ যেমন সেকালের হিন্দু বাঙালির প্রাণের ঠাকুর ও ভক্তের ভগবান, ঠিক তেমনি আবার তিনি সর্বশক্তিমান, বিশ্ববিধাতা, জগৎস্রষ্টা ও জগৎ নিয়ন্তা। তাঁর এই পরিচয়ের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল মহাভারতে প্রকাশিত কৃষ্ণের দৈবীসত্তার ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। কবি কাশীরাম দাস তাঁর রচনায় যুগপৎভাবে কৃষ্ণের দুই রূপেরই বর্ণনা করেছেন বলে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—তাঁর গ্রন্থে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের স্তূতি করে বলেছেন—
“অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অখি গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥”
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কাশীরামের এই বন্দনার সঙ্গে ভগবদগীতায় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বর্ণনার ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের এই ঐশ্বর্যরূপে সেযুগের বাঙালি বেশীক্ষণ তাঁকে আরাধনা করতে পারেনি। কারণ, এরফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে ব্যবধান সৃজিত হয়েছিল, সেটা তখনকার হিন্দু বাঙালির পক্ষে অসহনীয় ছিল। সেকালের বাঙালিরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যরূপের পরিবর্তে তাঁর আনন্দরূপকেই বেশি ভালোবাসতেন বলে তাঁদের কৃষ্ণ ‘অনাথের নাথ’ ‘নির্ধনের ধন’ এবং ‘সুখ দুঃখ কহিবার একমাত্র স্থান’ ছিলেন। এজন্যই তাঁর কাছে কাশীরামের বেদনা-বিধুর দ্রৌপদী নিজের দুঃখ নিবেদন করেছিলেন। তবে দুঃখ ও বেদনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবার আকাঙ্খায় কাশীরাম সৃষ্ট দ্রৌপদী যে এভাবে তাঁর কাছে নিজের মর্মবেদনা ব্যক্ত করেছিলেন—এমনটা কিন্তু নয়। বরং তিনি তাঁর আত্মার আত্মীয়ের কাছে নিজের ব্যথিত হৃদয়ের ভার লাঘব করে শান্তি পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি কি গভীর ভালোবাসা থাকলে তবেই তাঁকে এমনভাবে আপন করে নেওয়া যায়—একথা এখানে সহজেই অনুমেয়। আর ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসাই ভক্তকে অধিকারবোধ দান করে, এবং এই অধিকারবোধ থেকেই অভিমান সৃজিত হয়। একারণেই কাশীরামের সৃষ্ট দ্রৌপদীর উক্তির মধ্যে সুগভীর ভক্তির সঙ্গে সামান্য অভিমানের রেশও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—কবি তাঁর গ্রন্থের একজায়গায় লিখেছিলেন—
“এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃ স্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অবিরাম ঝরে॥
পুনঃ গদগদ কণ্ঠে বলয়ে পার্বতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি॥”
সেই সংসারে দ্রৌপদী একা এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছিলেন বলে তাঁর উপরে অত্যাচার হয়েছিল। তাই নিজের একান্ত আত্মীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত অভিমান প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এজন্যই দ্রৌপদী তাঁর কাছে এই ক্ষুব্ধ উক্তি করেছিলেন, এবং নিজের চোখের জল ফেলেছিলেন। এখানে দ্রৌপদীর অভিমান স্পষ্ট না হলেও এর অস্তিত্ব কিন্তু দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার মহাভারতে থাকা এধরণের অংশগুলিতে দ্রৌপদীর উক্তিতে অভিমানের সুর অনেক বেশি স্পষ্ট বলেই লক্ষ্য করা যায়। সেখানে দ্রৌপদী পরিষ্কারভাবেই বুলেছিলেন যে, তাঁর কেউই নেই, এমনকি কৃষ্ণও নেই (বনপর্ব, ১১-১২৬)। কিন্তু কাশীরাম দাসের সময়কার বাঙালি নারীর পক্ষে কৃষ্ণ নেই—একথা বলা সম্ভব ছিল না। কারণ, কৃষ্ণই তাঁর একমাত্র অবলম্বন ও চরম আশ্রয় ছিলেন। এপ্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের কৃষ্ণ হলেন দ্রৌপদীর একমাত্র সখা; আর একারণেই এই মানবিক সখ্য সম্বন্ধে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অভিমান সহজেই স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। ব্যাসদেবের রচনায় তাঁদের সম্বন্ধ একান্তভাবেই মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু অন্যদিকে কাশীরামের রচনায় মানবিক ভাব ও ভগবৎপ্রেম একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে এতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের প্রীতি-নির্ভর একটি অপূর্ব ভক্তির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—যা সেযুগের বাঙালির মানস বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করছে।
ইতিপূর্বে কাশীরামের রচনায় সেযুগের বাঙালি হিন্দুর যে জীবনবোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ঈশ্বরের কাছে শুধুমাত্র অহৈতুকী ভক্তি কাম্য হয়েছিল, সেটা কবির রচনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায় যে, রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠিরের করায়ত্ত হয়েছিল। তখন দেশের সমস্ত রাজা মহারাজা, এমনকি স্বর্গের দেবতারাও পর্যন্ত কৃষ্ণের মাহাত্ম্যে যুধিষ্ঠিরের চরণে নিজেদের প্রণাম জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের এই অপরিমেয় প্রাপ্তিতে যুধিষ্ঠির অহংকারে স্ফীত ও নিজের জীবনের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে যাননি। বরং যে ভক্তিস্নিগ্ধ শান্ত জীবনযাত্রা সপ্তদশ শতকের বাঙালির বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটাকে প্রকাশ করে গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজের প্রাণের অকপট কামনা ব্যক্ত করে বলেছিলেন—
“তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম॥
তড়িৎ জড়িত পীত কৌষেয় বসন।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বপু কৌস্তুভ ভূষণ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীক পাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু সর্বলোক নাথ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্যবান জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু তোমার চরণ॥
সে সব ভক্তের পদ বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্খায় মাগিবারে না করি ভরসা॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥
এ সব অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি॥”
এখানে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণের রূপ দর্শন করেছিলেন। প্রিয়জনের রূপ দর্শন এবং এর বর্ণনা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলে যুধিষ্ঠির এই আনন্দে মগ্ন হয়ে তাঁর দেবতার কাছে নিজের প্রাণের কামনা জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানে বিনয়ে বিগলিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, যেসব ভক্ত ঈশ্বরের চরণ নিত্যবন্দনা করেন এবং যাঁরা রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী, তিনি সেসব লাভ করবার ভরসা করেন না। কারণ, এসব মহাজনদের পক্ষেই লভ্য। একজন সাধারণ মানুষ হয়েই তিনি এসব ভক্তের পদ বন্দনা করতে অভিলাষী। এটাই তাঁর জীবনের কাম্য। যদিও তাঁর জীবনে প্রাপ্তিব কোন সীমা নেই, কিন্তু তিনি একথাও জানেন যে—‘এ সকল অনিত্য যেন বাদিয়ার বাজি।’ জীবনের একমাত্র নিত্য বা সার বস্তু হল ভক্তি, যে ভক্তিতে ঈশ্বরকে জন্ম জন্মান্তরে লাভ করা সম্ভব। আর তাই কাশীরামের যুধিষ্ঠিরের একমাত্র কামনা ছিল—‘অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ।’ এখানে সেকালের হিন্দু বাঙালির যে মনোভাব ও জীবনবোধ যুধিষ্ঠিরের এই উক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেটাকে যেন শ্রীচৈতন্যদেব বিরচিত ‘শিক্ষাষ্টকের’ অন্যতম দুটি শ্লোকের নির্যাস বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে মহাপ্রভু বলেছিলেন—
“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥”
অর্থাৎ—“তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, তরুর মত সহিষ্ণু হইয়া নিজে নিরভিমান হইয়া এবং সর্বজীবে সম্মান দিয়া সর্বদা হরিনাম করিবে।”
কাশীরামের যুধিষ্ঠিরও সমস্ত পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়েও এধরণের নম্র ও শান্তজীবনই কামনা করেছিলেন। এমনকি মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে জীবনের যে কামনা অভিব্যক্ত হয়েছে, কাশীরামের যুধিষ্ঠিরও সেই একই কামনা করেছিলেন—
“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥”
অর্থাৎ—হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দরী বা কবিতা কামনা করি না, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার ভক্তি থাকে।
কাশীদাসী মহাভারতেও যুধিষ্ঠিরের উত্তিতে এই শ্লোকের ভাব অত্যন্ত অকপট ও সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়—
“যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ॥”
একহিসাবে এটা অত্যন্ত সাধারণ ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যহীন কামনা ছিল। কারণ, ঈশ্বরে ভক্তিই সেযুগের সকলের কাছে কাম্য ছিল। কিন্তু বাংলায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে বাঙালি হিন্দুর সর্বজন চিত্তে এই ভক্তি এভাবে বিরাজমান ছিল না। তিনিই পার্থিব ধন-সম্পদের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আকাঙ্খাকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন এবং এই কামনায় তাঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন। এজন্যই দেখা যায় যে, আলোচ্যযুগের সাধারণ হিন্দু বাঙালির কামনাই কাশীরামের যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আবার ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিতে এই কামনা থেকে ভ্রষ্ট হওয়াও তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, যা কাশীদাসী মহাভারতে আত্মবিস্মৃত সত্যভামার দর্পচূর্ণের কথার মাধ্যমে সত্যভামার ব্রতপালনের কাহিনীতে প্রকাশিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর ভালোবাসার কারণে সত্যভামা মনে করেছিলেন যে, কৃষ্ণের উপরে শুধুমাত্র তাঁরই অধিকার রয়েছে। আর তাই পরজন্মে কৃষ্ণকে নিজের স্বামীরূপে লাভ করবার পুণ্যফলের লোভে সত্যভামা ব্রতপালন করেছিলেন এবং পুন্যফল লাভে এই ব্রত উদযাপন করবার জন্য নারদের কাছে কৃষ্ণকে দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেযুগের বাঙালি বৈষ্ণবের জীবনে কৃষ্ণই যে একমাত্র বস্তু ছিলেন, তিনি ছাড়া তাঁদের অন্য কিছুই যে ছিল না—সত্যভামা তাঁর জীবনের এই আদর্শকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই পরে নিদারুণ বেদনার মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নাম ও নামী হলেন অভিন্ন, তুলসীপত্রের কৃষ্ণ নাম আসলে কৃষ্ণেরই সমান এবং কোনও ধরণের পুণ্যের লোভে তাঁকে দান করা সম্ভব নয়।
কৃষ্ণের প্রতি এই যে সুগভীর ভক্তি, তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্খা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সাধক ভক্ত যে অবস্থায় উপনীত হন সেটাকে দিব্যদশা বলা হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যের জীবনে ভক্তির এই চরম প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত বহু গৌরচন্দ্রিকাতে শ্রীচৈতন্যের এই দিব্য রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেযুগের অন্যতম বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তা গোবিন্দদাস নবদ্বীপের সুরধুনী তীরে পরিভ্রমণরত গৌরাঙ্গের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন যে, কনককান্তি গৌরচন্দ্র সুরধুনী তীর উজ্জ্বল করে ভ্রমণ করছেন। তাঁর নয়ন থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে, এবং তাঁর দেহ কদম্ব কেশরের মতোই রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তিনি অহর্নিশি দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে বাহ্য জ্ঞানহারা হয়ে গিয়েছেন, এবং ভক্ত ভ্রমররা তাঁর চরণে ঝংকার করছেন। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের এই জাতীয় পদ যে কবি কাশীরামদাসকেও কতটা প্রভাবিত করেছিল, একথা তাঁর রচিত ছত্র থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যেমন—কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি একজায়গায় বলেছিলেন—
“কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হৈয়া কম্পিত শরীর॥
নয়ন যুগলে পড়ে বারিধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরু বীর॥”
এখানে কাশীরামের কৌরব বীর তাঁর বীর্যবত্তা প্রকাশ না করে নিজের গভীর ভক্তির পরিচয় দান করেছিলেন বলে দেখা যায়। এজন্যই একজন ভক্ত বৈষ্ণবের মত তাঁরও বারিধারায় নয়ন বিগলিত হয়েছিল, শরীরে কম্পের শিহরণ জেগে উঠেছিল, এবং তিনিও মুহূর্মুহ অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি কবি কাশীরামের রচনায় ঈশ্বরেরও পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল। ভক্তের এই ভালোবাসাতে তিনিও ভক্ত থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তিনিও ভক্তের চরণে নত হয়েছিলেন। তিনিও ভক্তের প্রতি ভালোবাসাতে আবদ্ধ ছিলেন। এজন্যই কাশীদাসী মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে বলেছিলেন—
“আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে।”
শুধু এটুকুই নয়, ঈশ্বর সমস্ত দুঃখ বিপদ থেকে ভক্তকে উদ্ধার করেন বিশ্বাসে মধ্যযুগের এই বাঙালি কবির রচনায় ভক্তের জন্য ঈশ্বরের মানবিক উদ্বেগটুকুও লক্ষ্য করবার মত। কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্বে দুর্বাসার আগমনে পাণ্ডবরা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, তখন দ্রৌপদীর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করে অরণ্যে পাণ্ডব সমীপে গমন করেছিলেন। এসময়ে রুক্মিণীর মৃদু অভিযোগের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—
“ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
কেবল আমার ভক্ত সুখ দুঃখ দাতা॥
ভক্তজন যথা মম থাকে দেবী সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়॥
সে কারণে ভক্তদুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত বৎসল॥”
এই ভক্ত ও ভগবানের কথা সংস্কৃত ভাষার মহাভারতেও প্রকাশিত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে কাশীদাসের রচনায় ঈশ্বর যদিও কৃষ্ণরূপে বিরাজমান, কিন্তু তবুও সেযুগের হিন্দু বাঙালির মনে কৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীও আসন গ্রহণ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাস বলে যে, সেযুগের বাংলায় গোষ্ঠীগত ধর্মসাধনায় এসব দেবদেবীর অনুগামীরা পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন, এবং তাঁরা তখন নিজেদের সাধন ভজনের জন্য পৃথক পৃথক পথ অনুসরণ করতেন; কিন্তু সেকালের সাধারণ বাঙালি হিন্দুর চেতনায় সমস্ত দেবতাই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। তখনকার বাঙালি হিন্দুর জীবনে, অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে শিব গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে বিরাজমান ছিলেন। গবেষকদের মতে, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি হিন্দুর চেতনাতে যে শিব বিরাজমান ছিলেন, তাঁর মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিক—এই উভয়বিধ ভাবেরই সংমিশ্রণ ঘটেছিল। মধুযুগের বাংলায় পুরাণের মহাদেব বাঙালির কুটিরে পদার্পন করে সেকালের সাধারণ বাঙালি হিন্দুর মতোই আচরণ করেছিলেন।
এজন্যই সেযুগের হিন্দুঘরের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের মতোই মঙ্গলকাব্যসমূহেও হরগৌরীর কলহের বিবরণ পাওয়া যায়। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, কবি কাশীরাম দাসও এই ধাবায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে হরগৌরীর কলহের সরল বিবরণ দান করে বাঙালি হিন্দুর দাম্পত্য মাধুর্যের সঞ্চার করেছিলেন এবং নিজের সৃষ্ট মহাভারত কাহিনীকে মানবিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।
তৎকালীন বাংলায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—এই তিনটি সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। সেযুগে শৈব ও শাক্তের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দুর সমন্বয়ী চেতনাতে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের সন্ধানও পাওয়া যায়। একইরমভাবে কবি কাশীরাম তাঁর সৃষ্ট সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে মোহিনীরূপী নারায়ণ ও মহাদেবের মিলিত রূপের যে বর্ণনা দান করেছিলেন, তাতে যেমন হরি ও হরের মিলনের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণবের মিলনের কথা প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার অর্ধ-নারীশ্বর রূপের মধ্যে শৈব ও শাক্তের মিলনের কথাও অভিব্যক্ত হয়েছিল।
তখনকার বাঙালি হিন্দুর জীবনে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে লক্ষ্মীর একটি বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল বলে কাশীদাসী মহাভারতের সমুদ্রমন্থন কাহিনীতে এই গুরুত্ব এবং লক্ষ্মীর প্রতি বাঙালি হিন্দুর চিত্তের সুগভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, ব্যাসদেবের মহাভারতে এই কাহিনীতে অমৃত লাভ করাই যেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালি কবির রচনায় সেখানে বিবৃত হয়েছিল যে, অমৃত নয়, বরং লক্ষ্মী লাভই সমুদ্রমন্থনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এটা সেযুগের বাঙালি হিন্দুর মনের অন্যতম আকাঙ্খাকে প্রকাশ করেছিল।
এসব ছাড়া উভয় মহাভারতের চরিত্র-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করলেও দেশ ও কালের সর্বাধিক প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের পাত্রপাত্রীসমূহ প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ অথবা ক্ষত্রিয় রমণী ছিলেন বলে দেখা যায়। একারণেই তাঁদের শৌর্য, বীর্য, আত্মসম্মানবোধ, প্রতিহিংসা প্রবণতা, এবং তেজস্বিতায় ক্ষাত্র পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু কবি কাশীরাম দাসের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আচ্ছন্ন হয়ে বাঙালিসুলভ কোমলতা ও ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। একইরকমভাবে সংস্কৃত ভাষার মহাভারতে যেসব চরিত্র সত্যিকারের রাজকীয় গুণে ভূষিত হয়ে রাজমহিমায় বিরাজমান রয়েছে, কাশীরাম দাসের রচনায় সেসব চরিত্র রাজবেশে সজ্জিত হলেও প্রকৃতির বিচারে সাধারণ হিন্দু বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ কাশীদাসী মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রেই রোদনশীলতা, বাঙালিসুলভ কোমলতা এবং তৎকালোচিত ভক্তিভাব প্রকাশিত হয়েছে। আর একারণেই সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের যুধিষ্ঠির কবি কাশী দাসের রচনায় জ্ঞাতিশত্রু নিগৃহীত ধর্মভীরু সাধারণ বাঙালি হিন্দুতে পরিণত হয়ে গিয়েছেন; আর অন্যদিকে দুর্যোধন এখানে কোন প্রতিষ্ঠাকামী বীর নৃপতি নন, বরং সাধারণ পরস্বঅপহারী একজন দুর্বৃত্তমাত্র। প্রাচীন ভারতের একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের তেজ ও দর্প দুর্যোধন চরিত্রকেও যে মাঝে মাঝে কিভাবে মহিমান্বিত করেছিল, একথা সংস্কৃত ভাষার মহাভারত অনুধাবন করলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এমনকি এতে দুর্যোধন সহায়ক রাজা কর্ণের চরিত্র মহিমাও অদ্বিতীয় বলে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পুরুষকারের সঙ্গে প্রতিকূল অদৃষ্টের সংগ্রামে মহিমময় এই চরিত্রে সংস্কৃত ভাষার মহাভারতে যে রাজটীকা লাঞ্ছিত হয়েছিল, কবি কাশীরাম দাসের রচনায় এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বরং এতে তিনি দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনের সহায়কমাত্র বলেই দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি উভয় মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অন্যান্য পাণ্ডবদের চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। ব্যাসদেবের মহাভারতের ভীম চরিত্রের মধ্যে যে রূঢ় ভাষণ, কঠোরতা ও তেজ প্রকাশিত হয়েছে, সেটা কিন্তু কবি কাশীরামের মহাভারতে পাওয়া যায় না। বরং তাঁর রচিত মহাভারতে ভীমের রুঢ়তা বহুলাংশে প্রশমিত, বীর্যবত্তা আতরঞ্জনে অস্বাভাবিক ও হাস্যকর, এবং ঔদরিকতা ক্ষাত্র মহিমা বিসর্জিত বলে দেখা যায়। এছাড়া সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের অর্জুন অতীতের একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মতোই নিজের বাহুবলে নির্ভরশীল হলেও কাশীদাসের মহাভারতে তিনি কিন্তু কৃষ্ণ মহিমায় আত্মনিবেদিত একজন ভণ্ড বৈষ্ণব বাঙালিমাত্র। তবে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণ চরিত্রে সর্বাধিক রূপান্তর সাধিত হয়েছিল বলে লক্ষ্য করা যায়।
এছাড়া সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের পুরুষ চরিত্রগুলির মতোই নারী চরিত্রসমূহও দেশ ও কালের প্রভাবে কাশীদাসী মহাভারতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল বলেই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ আদি মহাভারতে যেসব তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণীর সন্ধান পাওয়া যায়, কবি কাশীরাম দাসের রচনায় কিন্তু তাঁদের বাঙালি রমণীরূপেই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সহধর্মিনী, এবং বংশ গৌরবে ও স্বামী সৌভাগ্যে সচেতনা তেজস্বিনী একজন ক্ষাত্র রমণী ছিলেন। যদিও বিভিন্ন সময়ে অপমানে ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেবের মহাভারতে এই ক্রন্দনের সঙ্গে তাঁর কন্ঠে ক্রোধের গর্জনও শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। অন্যদিকে কবি কাশীরাম দাসের রচনায় দ্রৌপদী হলেন একজন অনাথা অসহায়া দুর্বল বাঙালি হিন্দু রমণী, যিনি আত্মবিলাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পাওয়ার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করেছিলেন। কাশীরামের বাঙালি দ্রৌপদীর মতোই কুন্তীও তাঁর রচনায় একজন অসহায়া বিধবা, ভাগ্য বিড়ম্বিতা ও জ্ঞাতিশত্রুর হাতে নির্যাতিতা বাঙালি জননীমাত্র। আসলে কাশীরামের রচনায় দেশ ও কালের প্রভাবে আসল মহাভারতের চরিত্রসমূহের এমনধরণের রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। এজন্যই উভয় গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, যদিও এগুলির চরিত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু এই আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই চরিত্রগুলিতে প্রকৃতিগত ব্যবধানও সৃজিত হয়েছে। বস্তুতঃ জীবনবোধের পরিবর্তনের জন্যই এই উভয় মহাভারতে চারিত্রিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে, এবং দেশ ও কালগত প্রভাবে উভয়ক্ষেত্রে এই জীবনবোধের পবিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্যাসদেবের কালে নিজের বাহুবল প্রকাশ করে শৌর্যে ও বীর্যে অনন্য হওয়াই ক্ষত্রিয়দের কাছে জীবনের লক্ষ্য ছিল। তখন যিনি অস্ত্রসন্ধানে নিপুণ হতেন, আর রণক্ষেত্রে যাঁর বাহুবল অন্য সকলকে পরাভূত করতে পারত, তিনিই সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকতেন। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত থাকা এধরণের শক্তিমত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাই সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের চরিত্রসমূহের অন্তরতম কামনারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। একারণেই এতে দেখা যায় যে, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা বা তৎকালীন দেশের শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করবার আকাঙ্খাই দুর্যোধন চরিত্রের সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এমনকি এখানেই সংস্কৃত ভাষার আদি মহাভারতের কর্ণ চরিত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজের নীচের দিকে থাকা সুতপুত্রের পরিচয়কে নিজের একমাত্র পরিচয় বলে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে দমন করেই তাঁকে তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি একথাও জানতেন যে, তাঁর বিরুদ্ধ ও সহানুভূতিহীন যে জগৎ তখন অর্জুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, সেই জগতেও তাঁকে অর্জুনের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করতে হবে। আর এই প্রমাণ শুধু আত্মশ্লাঘার দ্বারা করলে চলবে না, কর্মক্ষেত্রে অপরিমিত বীরত্বের মাধ্যমেই করতে হবে। এমনকি আদি মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, দুর্যোধনেব সমস্ত রাজ্য অধিকার করবার জন্যই তিনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্যাসদেবের মহাভারতের এসব বীর ক্ষত্রিয়রা রণক্ষেত্রে পরস্পরকে স্পর্ধা করেছিলেন, আর প্রতিপক্ষের আঘাতে আহত হয়ে কিছুতেই সেই আঘাতকে স্বীকার করতে পারেননি বলেই দ্বিগুণ শক্তিতে প্রতি-আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। একারণে আদি মহাভারতের সামান্যতম চরিত্রও নিজের বাহুবলে, আত্মসম্মানে, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাতে এবং আত্মপ্রকাশের বাসনাতে উজ্জ্বল বলেই দেখতে পাওয়া যায়।
কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই জীবনবোধ—মধ্যযুগের কবি কাশীরাম দাসের কালে ছিল না বলে শক্তিমত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের পরিবর্তে ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে আত্মনিবেদন করাই তাঁর সময়কার মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তখন অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তাঁকে পুনরাঘাত করবার পরিবর্তে সেই আঘাত ক্ষমা করে দেওয়াই সাধারণ নিয়ম ছিল। আসলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে এসময়কার বাঙালি হিন্দুদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বাঁধা ছিল, যা সংস্কৃত ভাষার মহাভারতে প্রকাশিত জীবনবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এসময়কার বাঙালি হিন্দুদের জীবনবোধ বৈষ্ণব ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই ভাবধারার মূল এটাই ছিল যে, বৈষ্ণব চেতনায় সর্ব অহংকার বিসর্জন দিয়ে নিজেকে দীনাতিদীন বলেই মনে করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ পুনরায় স্মরণীয় যে, ‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা’—মহাপ্রভুর উপদেশ ছিল। সুতরাং অন্যের আঘাতে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে তাঁকে প্রতিআঘাত করলে চলবে না; তরুর মত অপার সহিষ্ণুতায় এবং শিশুর প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা,—সেই ভালোবাসায় তাঁকে ক্ষমা করতে হবে,—কাশী দাসের সময়ে এটাই যাঁদের জীবন বাণী ছিল, তাঁদের পক্ষে কিছুতেই সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের চরিত্রসমূহের জীবনবোধ স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। একারণেই সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের প্রতি আঘাত ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে মধ্যযুগের বাঙালি কবির রচনায় সমকালীন বাঙালি হিন্দুর প্রেম ও ক্ষমার কথাই প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি এতে অহংকারকে সর্বপ্রযত্বে বর্জন করবার কথাও বলা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কবি কাশীরাম দাস সংযোজিত ‘অকাল আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ’ কাহিনীতে দ্রৌপদীর অহংকার কিভাবে চূর্ণ হয়েছিল, এর একটা বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত ঘোষ যাত্রায দ্বন্দ্ব কলহের থেকে প্রেম ও ভালোবাসার কথা স্বয়ং দুর্যোধন কণ্ঠে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলেও দেখতে পাওয়া যায়। এই অংশে দেখা যায় যে, দুর্যোধনসহ সব কৌরব নিগৃহীত হলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডবেরা তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। আর তখন যুধিষ্ঠিরের এই মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে দুর্যোধন বলে উঠেছিলেন—
“পূর্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ ঘটিবে॥
ভীমার্জুন হৈতে মোরে তাঁর স্নেহ অতি।
যতনে পালিত মোরে ধর্ম নরপতি॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাই করিনু বিশ্বাস॥”
সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের কোথাও কিন্তু দুর্যোধনের কন্ঠ থেকে এধরণের কোন উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ, সেখানে এধরণের বক্তব্য তাঁর মূল প্রকৃতির পরিপন্থী। কিন্তু কাশীরামের দুর্যোধন একথা সহজেই বলতে পেরেছিলেন যে, ভীমার্জুন থেকেও তাঁর প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভালোবাসা বেশি! আসলে সংস্কৃত ভাষার মহাভারতের বিরোধ ও সংগ্রাম মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দুর মানসিক আবহাওয়ার অনুকূল ছিল না। আর খুব সম্ভবতঃ এজন্যই মধ্যযুগের বাংলায় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ রামায়ণের ঢের পরে শুরু হয়েছিল। আর এই অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব এটাই ছিল যে, তিনি যুগচেতনার অনুগামী হয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারতের মত একটা প্রাচীন গ্রন্থের ভাবগত পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন।
সূত্র: ফেসবুক























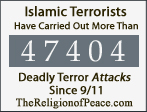




0 Comments