প্রাচীন ভারতে দীর্ঘসময় ধরে চরকসংহিতা প্রচলিত থাকবার ফলে একটাসময়ে সেযুগের বিভিন্ন চিকিৎসক ও টীকাকারদের হাতে পড়ে এই সংহিতা গ্রন্থটির অঙ্গহানি ঘটেছিল। এসময়ে গ্রন্থটিতে কোথাও যেমন নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার কোন কোন জায়গা থেকে মূল্যবান তথ্যগুলিকে বাদও দেওয়া হয়েছিল। এরফলে কোন একসময়ে চিকিৎসকদের স্বার্থেই চরকসংহিতা নামক গ্রন্থটি সংস্কার করবার প্রয়োজন অনুভূত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনকার বহু মনীষী এই গ্রন্থটিকে সংস্কার করবার কথা চিন্তা করলেও শেষপর্যন্ত তাঁদের মধ্যে কেউই এই দুরূহ কাজে নিজের হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হতে পারেননি। তবে অবশেষে আয়ুর্বেদাচার্য দৃঢ়বলের প্রচেষ্টায় ও যত্নে চরকসংহিতার নবরূপায়ণ ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দৃঢ়বল একদিকে যেমন একজন সুচিকিৎসক ছিলেন, ঠিক অন্যদিকে তেমনি আবার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিতও ছিলেন। তাই তিনি শুধু চরকসংহিতাকে সংস্কার করেই ক্ষান্ত হননি, এতে নবাবিষ্কৃত বহু তথ্যও সংযোজন করেছিলেন। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে চরকসংহিতা নামে যে গ্রন্থটি প্রচলিত রয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে চরক ও দৃঢ়বল—উভয়েরই রচনা। তবে এখনকার গ্রন্থের মধ্যে কোন অংশটি যে চরক রচনা করেছিলেন, এবং কোনটি যে দৃঢ়বলের রচনা—এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই নয়, ঐতিহাসিকদের মতে, অতীতে যে চরকসংহিতাটি দেশ-বিদেশে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়েছিল, সেটিও আদতে আচার্য দৃঢ়বলের দ্বারা সংস্কার করা চরকসংহিতাই ছিল।
কিছু পণ্ডিতের মতে, দৃঢ়বল কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আবার কিছু পণ্ডিতের মতে তাঁর জন্মস্থান হল পাঞ্জাব। তবে তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া চরকসংহিতার সংস্কার করা ছাড়া তিনি নিজের কোন মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেননি বলে গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তবে তাঁকে নিয়ে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, তিনি পতঞ্জলির বহু পরে এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন; আর চরক সংহিতার সংস্কারক হিসাবেই তিনি ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে নিজের একটা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিতে পেরেছেন।
এভাবে আচার্য দৃঢ়বলের পরে আরও কয়েকশো বছরের মধ্যে ভারতে চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতার অনুরূপ আরও বহু সংহিতা রচিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তখন চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলে কিছু কিছু অজ্ঞাতনামা লেখক নিজেদের গ্রন্থকে চরকসংহিতা বা সুশ্রুতসংহিতা নাম দিয়েও চালিয়ে দিয়েছিলেন। এরফলে একসময়ে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যখন আসল চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতাকে চিহ্নিত করবার আর কোন উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, এসব জাল গ্রন্থের কারণে প্রাচীন চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা এবং পরবর্তীকালের আরও কয়েকটি জনপ্রিয় সংহিতাগ্রন্থ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভারতে মধ্যযুগের শুরু হয়েছিল; আর মধ্যযুগের ভারতে প্রাচীনকালের এসব লুপ্তপ্রায় গ্রন্থকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য যেসব পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য বাগভট অন্যতম ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে কঠোর পরিশ্রম করবার পরে প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি উদ্ধার করে সেগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি, এবং নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা একইসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে ‘অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ’ নামের একটি মহান আয়ুর্বেদগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত এই গ্রন্থটি মূলতঃ চিকিৎসা সংগ্রহ সার। এবং আজও সর্বত্র এই প্রাচীন গ্রন্থটির সমাদর দেখতে পাওয়া যায়।
কিন্তু ‘অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ’ গ্রন্থটি থেকে ঐতিহাসিকেরা এর লেখক সম্বন্ধে এখনো পর্যন্ত অতি অল্প তথ্যই উদ্ধার করতে পেরেছেন। এই গ্রন্থলেখক নিজেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁর নাম হল বাগভট, জন্মস্থান হল সিন্ধুদেশ এবং পিতার নাম হল সিংহগুপ্ত। এছাড়া সমকালীন ইতিহাস থেকে বাগভট সম্বন্ধে অন্যান্য যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেসব থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর যৌবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু অবলোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন; আর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পরে তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এথেকে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার আগে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং এমনকি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পরেও উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে নিজের গবেষণা অব্যাহত রেখেছিলেন।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের ভারতে আগত প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎসিং–এর বিবরণীতেও বাগভট নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বাগভট নালন্দার একজন আচার্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; এছাড়া ইনি ঈৎসিং–এর গুরুও ছিলেন। এথেকে অনেকে অনুমান করেন যে, চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎসিং–এর গুরু বাগভট এবং ‘অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ’ গ্রন্থের রচয়িতা বাগভট আসলে একই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে বাগভটকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি বলে মনে করবার সঙ্গতঃ কারণ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, ঈৎসিং–এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন; এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করবার পরে তিনি পদব্রজে রাজগৃহ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। সেসময়ে নালন্দার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে এরপরে ঈৎসিং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে একদিন ছাত্ররূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিজের বিবরণীতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, এসময়ে নালন্দার তরুণ আচার্য বাগভটের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, নালন্দার এই তরুণ আচার্য আবার চিকিৎসাশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। বাগভটই তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, এবং এজন্যই নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার পরে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন। ঈৎসিং জানিয়েছিলেন যে, তিনি ২২ বছর ধরে ভারতে অবস্থান করেছিলেন, এবং তারপরে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। এই বিবরণী থেকে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, বাগভট দীর্ঘকাল ধরে নালন্দার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সেখানকার তৎকালীন আচার্যদের মধ্যে তিনিই তখন বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেনি বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া ঈৎসিং যেহেতু বাগভট রচিত কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ করেননি, সেহেতু ‘অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ’ নামক গ্রন্থটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তবে তিনি ঠিক কত খৃষ্টাব্দে যে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, একথা নিজের গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেননি।
এই ‘অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ’ ছাড়াও ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়’ নামের আরেকটি গ্রন্থের রচয়িতার নামও বাগভট বলে দেখতে পাওয়া যায়। যদিও অতীতের কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, এই ‘অষ্টাঙ্গহৃদয়’ আসলে অন্য কোন বাগভটের লেখা, কিন্তু তবুও পরবর্তীসময়ের ভারতীয় গবেষকরা তাঁদের এই মতের সাথে সহমত হতে পারেননি। কারণ, তাঁদের মতে, এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে ভাষাগত যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি এই গ্রন্থের লেখকও নিজেকে সিংহগুপ্তের পুত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন বলেই দেখা যায়।
তবে একইসাথে মধ্যযুগের ইতিহাস একথাও বলে যে, তখনকার ভারতে আরেকজন বাগভটের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটেছিল। এমনকি তিনি ‘রসরতুসমুচ্চয়’ নামের একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, এই বাগভট অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে দু’জন বাগভটের নাম পাওয়া যায় বলে, ঐতিহাসিকেরা নালন্দার আচার্য এবং অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহের রচয়িতাকে ‘বৃদ্ধ বাগভট’ নামে অভিহিত করে থাকেন।
অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ গ্রন্থটি সুবৃহৎ ও সুমহান একটি গ্রন্থ। এই সমগ্র গ্রন্থটি ছ’ভাগে বিভক্ত; যথা—সূত্রস্থান, শরীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান। এমনকি এই গ্রন্থটিতে শল্যচিকিৎসার কথাও পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং গদ্য পদ্যময় হওয়ার কারণে এটি তত্ত্ব কিংবা কবিত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে বাগভট তাঁর এই গ্রন্থে যা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, সেটা সব জায়গায় স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মধ্যযুগের ভারতের শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসক—উভয়ের কাছেই এটি একসময়ে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া এই গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এতে থাকা ভূতবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা। এমনকি চরক ও সুশ্রুতর গ্রন্থেও এবিষয়ে এত বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। বাগভট ভূতাবেশকে উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বাগভট রচিত আয়ুর্বেদ সংগ্রহ গ্রন্থটি এককালে সারা ভারতে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও রয়েছে।
এরপরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যেসব বাঙালি পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাধবকর অন্যতম ছিলেন। ইনিও একজন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার নাম হল ‘রুগবিনিশ্চয়’; এবং এটি এককালে শুধুমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষে নয়, আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ আরবের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফা হারুণ অল রসিদের আগ্রহাতিশয্যে ‘রুগবিনিশ্চয়’ বা ‘মাধবনিদান’ নামক গ্রন্থটি পারসিক ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পরে ভারতে রচিত যেসব আয়ুর্বেদ গ্রন্থগুলি বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে মাধবের গ্রন্থটিই ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মাধব তাঁর গ্রন্থে বাগভটের কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করে থাকেন যে, মাধব বাগভটের পরে এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
তবে বস্তুতঃ ভারতের ইতিহাসে তিনজন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন শ্রীমাধব, দ্বিতীয়জন হলেন মাধবাচার্য, এবং তৃতীয়জন হলেন মাধবকর। এঁরা তিনজনই পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাস বলে যে, শ্রীমাধব সুশ্রুতসংহিতার একজন প্রাচীন টীকাকার ছিলেন, এবং মাধবকরের বহু আগেই এদেশে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্যদিকে মাধবাচার্য একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ—মাধবাচার্য মাধবের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও শ্রীমাধব এবং মাধব—এই দু’জনেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রকার ছিলেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে মাধবাচার্য কোন আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেননি বলেই অনেকে বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে মাধবাচার্য কোন আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ না হলেও মধ্যযুগের ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি মধ্যযুগের দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের গুরু এবং প্রধানমন্ত্রী, এবং ভারত প্রসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদের ভাষ্যকার মহাত্মা সায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মায়ন এবং মায়ের নাম ছিল শ্রীমতী। শৈশবেই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, এবং এরপরে দীর্ঘকাল ধরে শৃঙ্গেরীর মঠে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এসময়ে তিনি বিদ্যারণ্য স্বামী নামে সাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। মাধবাচার্যের আরেকজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ, তাঁর সময়কার একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। আয়ুর্বেদ বিষয়ে কিছু না লিখলেও মাধবাচার্য একাধিক বিষয়ে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব-দর্শনসংগ্রহ, জৈমিনীয়্যায়মালা, পঞ্চদশী, উপনিষদের টীকা এবং শঙ্করবিজয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বাঙালি মাধব বা মাধবকরের এমন বহুমুখী প্রতিভা না থাকলেও, তিনি তাঁর ‘রুগবিনিশ্চয়’ বা ‘মাধবনিদান’ নামক গ্রন্থটির জন্য ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়া ‘রত্নমালা’ নামের আরও একটি গ্রন্থও মাধবের নামে প্রচলিত রয়েছে; তবে এই গ্রন্থটি কতগুলি দ্রব্যগুণের পরিচয়মাত্র বলে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য নয়।
এরপরেও ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন যে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল, একথার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এমনকি মোঘলসম্রাট আকবরের আমলেও ভারতে কিছু কিছু আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচিত হয়েছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। বস্তুতঃ ইতিহাস বলে যে, সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর—উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও বহুশাস্ত্রে উৎসাহী ছিলেন, আর জাহাঙ্গীর শিক্ষিত ছিলেন বলে অবসর সময়ে বসে গ্রন্থ রচনা করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, মধ্যযুগের ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এই দুই মোঘল সম্রাটেরই যথেষ্ট দান রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় মোঘলযুগে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, ভারতীয় গণিত এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র কিছু কিছু বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু একইসাথে এসময়কার ইতিহাসে ভারতীয় মনীষার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ যদিও আকবরের অকৃত্রিম বন্ধু আবুল ফজল, আবুল ফজলের ভাই ফৈজী, স্বয়ং জাহাঙ্গীর, বাবর কন্যা গুলবদন এবং পরবর্তীকালে শাহজাহান পুত্র দারাশিকো ও সম্রাটদুহিতা জাহানারা, ঔরঙ্গজেবের দুহিতা জেবউন্নিসা খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ভারতের ইতিহাসে নিজস্ব প্রতিভার কিছুটা ছাপ রেখে গিয়েছেন বলে দেখা যায়, কিন্তু তবুও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এঁদের রচনা শুধুমাত্র সমকালীন সাহিত্য ও ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করেছিল। এসময়কার ভারতে প্রাচীন ঐতিহ্য-সম্পন্ন আয়ুর্বেদশাত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে তেমন কোন গবেষণা আদৌ হয়নি বলা যেতে পারে।
আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই সম্রাট আকবরের সময়ের ভারতের ইতিহাসে শুধুমাত্র একজন আয়ুর্বেদ সংগ্রহকারের নাম পাওয়া যায়; তিনি ছিলেন পণ্ডিত ভাবমিশ্র। ঐতিহাসিকদের মতে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে কান্যকুব্জ দেশের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতামাতার নাম ইতিহাস থেকে জানা যায় না। তবে তাঁর রচিত একটি সংগ্রহ-গ্রন্থের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, এসময়ের ভারতে প্রচলিত আয়ুর্বেদশাস্ত্র তাঁর হাতেই পুনরায় নবকলেবর প্রাপ্ত হয়েছিল।
মোঘল সম্রাট আকবরের সময়কার ভারতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ভাবমিশ্র আবির্ভাবের কিছুকাল আগে থেকেই ভারতে বিদেশী বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, আর তাঁদের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে তখন কিছু বিদেশী রোগও বিস্তারলাভ করেছিল। এর আগে রচিত প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এসব বিদেশী রোগের কোন বিবরণ ছিল না বলে পণ্ডিত ভাবমিশ্রই তখন এসব বিদেশী রোগের কথা নিজের গ্রন্থের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন, এবং এমনকি এসব থেকে প্রতিবিধান করবার উপায়ের নির্দেশও দিয়েছিলেন। ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে সেযুগে বিদেশ থেকে আগত এই রোগগুলিকে ‘ফিরিঙ্গী রোগ’ নামে বর্ণনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থে কিছু কিছু ‘যাবনিকা’ দ্রব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়; আর তিনি এমন কিছু কিছু ভেষজের কথাও উল্লেখ করেছিলেন যেগুলি তখন ভারতের মাটিতে জন্মাত না।
ঐতিহাসিকদের মতে পণ্ডিত ভাবমিশ্র খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং তিনি তাঁর গ্রন্থটি শেষ বয়সে রচনা করেছিলেন। তবে তিনি কোন মোঘল সম্রাটের অনুগৃহীত ছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন না।
দুৰ্ভাগ্যজনক হলেও ইতিহাসগতভাবে একথা সত্যি যে, পণ্ডিত ভাবমিশ্রের পরে ভারতে আর আয়ুর্বেদের অনুশীলন হয় নি। এজন্য তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকটাই দায়ী ছিল। বস্তুতঃ এসময়ের মধ্যেই বহু প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস বলে যে, ভাস্করাচার্য যেখানে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের শেষ কর্ণধার ছিলেন, পণ্ডিত ভাবমিশ্র সেখানে প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ জগতের শেষ মনীষী ছিলেন। তাঁর আগে তৈলবিহীন প্রদীপের মতোই ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রও অতি ম্লান শিখায় কিছুকাল যাবৎ অল্প অল্প আলো বিতরণ করে আসছিল, যা এরপরে ভাবমিশ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎই দপ করে নিভে গিয়েছিল।
সূত্র: ফেসবুক

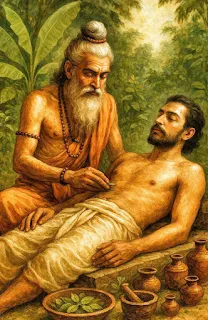





















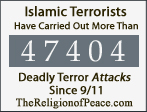




0 Comments