April 15, 2022 সপ্তডিঙা, সপ্তডিঙা নববর্ষ ১৪২৯, অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ISSN 2395 6054
ডঃ তমাল দাশগুপ্ত
প্রস্তাবনা
বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ব্যবহার বন্ধ হয়ে মোটামুটি পাঁচশো খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সৌরনির্ভর সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের (সূর্যসিদ্ধান্ত) ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল ভারতে, মেঘনাদ সাহা দ্রষ্টব্য। বর্তমানে দক্ষিণে তামিল থেকে পূর্বে বাঙালি জাতি যে নববর্ষ পালন করে, আর্যাবর্তের (বিহার থেকে হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড থেকে মধ্য প্রদেশঃ মোটামুটি উত্তর ভারত) বাইরে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে (এবং ভারতের বাইরেও এশিয়ার কিছু কিছু স্থানে) ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় সেই বৈশাখী নববর্ষের কোনও একটি আদিতম ফরম্যাট দেখা গিয়ে থাকতে পারে এই সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রভাবে। কারণ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রচলনকালে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পয়লা বৈশাখ মহাবিষুব সংক্রান্তির (Vernal Equinox) দিন (২২শে মার্চ) পড়েছিল, অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ হয়েছিল ২২শে মার্চ। এবং এটাই সূর্যসিদ্ধান্তের নির্দেশঃ মহাবিষুব থেকেই নতুন বছরের গণনা করতে হবে। বৈশাখী নববর্ষের সঙ্গে মহাবিষুব সম্পর্ক ঐতিহাসিকঃ বিহু থেকে বিষু নামে এই নতুন বছরকে বিভিন্ন স্থানে অভিহিত করা হয়, যে নামগুলি বিষুব স্মৃতিবাহী।
এই মহাবিষুব ও পয়লা বৈশাখ একই দিনে সমাপতনের ঘটনা গৌড়ের প্রথম লিপিবদ্ধ উত্থানের কাছাকাছি সময়ে ঘটে। গৌড়ের প্রথম পাথুরে লিপিবদ্ধ উল্লেখ ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, ঈশানবর্মার হড়াহা লিপি থেকে পাওয়া যাচ্ছে (গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্)। তবে অনুমান করা যায় দক্ষিণ পুণ্ড্র অঞ্চলে কিছু আগে থেকেই গৌড়ের উত্থানের জমি তৈরি হচ্ছিল, কারণ মালদা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের শ্রীগুপ্ত মগধে গিয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপন করবেন ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ।
আমি গৌড়ের উত্থান এবং প্রাচীন ভারতে তন্ত্রধর্মের নথিবদ্ধ বিস্তার একই সময়ে ঘটেছে বলে প্রমাণ পেয়েছি। আমাদের মাতৃধর্মের সেমিনাল টেক্সট শ্রীশ্রীচণ্ডী ষষ্ঠ শতকে রচিত।
এবং মহাবিষুবের ক্ষণে বৈশাখী নববর্ষের প্রচলন ভারতের অবৈদিক ব্রতধর্মী তন্ত্রাশ্রয়ী সভ্যতায় মোটামুটি ওই একই সময়কালে ঘটেছে।
এগুলি পরস্পর সম্পর্কিত, এই প্রবন্ধে আমরা দেখব। অতি দ্রুত এটি লিখতে হচ্ছে সপ্তডিঙা নববর্ষ ১৪২৯ সংখ্যার জন্য, অতএব এটিকে পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে একটি নতুন রূপ দেওয়ার ইচ্ছে থাকল, কিন্তু আপাতত যেটুকু বলা যাচ্ছে সেটুকু লিপিবদ্ধ থাক। সময়স্বল্পতাজনিত খামতি থাকতে পারে, সব কথা বলে ওঠা যাবে না সম্ভবত।
এক
সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে বৈশাখী নববর্ষের প্রচলন, তার একটা সমস্যা হল, মেঘনাদ সাহা বলছেন, সূর্যসিদ্ধান্ত যে বছরের হিসেব দেয়, তা ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিনের। কিন্তু একটি সৌর বর্ষের প্রকৃত দৈর্ঘ্য হল ৩৬৫.২৪২১৯৬ দিনের। অতএব .০১৬৫৬ দিনের একটা ব্যবধান থাকছে প্রতি বছরে। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মহাবিষুব ২২শে মার্চ, এবং সেদিন পয়লা বৈশাখ হয়, এরপর পরবর্তী ১৪০০ বছরে কিন্তু পয়লা বৈশাখ মহাবিষুব থেকে সরে এসেছে ২৩.২ দিন, মেঘনাদ সাহা বলছেন। আজ পনেরোশো বছর অতিক্রান্ত। এই একবিংশ শতকে আমাদের বঙ্গাব্দ এখন মূলত ১৪ বা ১৫ এপ্রিল শুরু হয়।
এই সূর্যসিদ্ধান্তনির্ভর গণনার ত্রুটি কিছুটা অয়নচলনের জন্য (পৃথিবীর নিজস্ব আহ্নিক ও অক্ষীয় গতির কারণে)। কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্ত গণনায় জ্যোতির্বিদ্যার দক্ষতা দরকার, বলা বাহুল্য। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র নামে একটি সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতে এই বর্ষগণনার কাজ করতেন, মেঘনাদ সাহা জানাচ্ছেন। আমরা জানি এরকম পেশাভিত্তিক কাস্ট তন্ত্রধর্মের কুলশীলপ্রথার অনুগামী।
প্রসঙ্গত এঁরা যাগযজ্ঞও করতেন এবং সূর্যের রশ্মির নানা প্রয়োগে কুষ্ঠরোগ-সহ অন্যান্য চর্মরোগের উপশমের দাবি রাখতেন। সৌর উপাসকদের সঙ্গে চর্মরোগ প্রশমনের সম্পর্ক আছে, শাম্বের কাহিনীটি দ্রষ্টব্য। আমরা জানি শেষ বয়সে গৌড়সম্রাট শশাঙ্কের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, তখন এঁরা গৌড়ে এসেছিলেন যাগযজ্ঞ করতে, এঁদের কুলজী গ্রন্থে সেই উল্লেখ আছে। যেহেতু শশাঙ্কের কুষ্ঠরোগের উল্লেখ শশাঙ্কের শত্রু ও নিন্দুক হিউয়েন সাংও করে গেছেন, তাই এই গ্রহবিপ্র দাবি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন নেতিবাচক মনোভাব নেন নি, বরং ইতিহাসের সত্যতার মর্যাদা দিয়েছেন।
শশাঙ্কযুগে বাংলায় আগত গ্রহবিপ্র সমাজ কি এঁদের সঙ্গে এই বৈশাখী নববর্ষের বর্ষগণনার পদ্ধতি বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন? সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না।
অনেক সময়েই অব্দের প্রয়োগে রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট বা অতীতের বছরগুলিকে বিন্যাস করার বর্তমান প্রয়াস দৃশ্যমান হয়। তাই শশাঙ্কের রাজত্বের প্রথম বছরকে কেন্দ্র করে অব্দের সূচনা শশাঙ্কের রাজত্বের শেষের দিকেও হওয়া সম্ভব। ইতিহাসে এমন অনেক নিদর্শন আছে। তাই শশাঙ্কের রোগ শান্তির জন্য আগত শাকদ্বীপি গ্রহবিপ্রদের সময়কাল শশাঙ্কের রাজত্বের শেষের দিকে হলেও তাদের প্রভাবে সৌর বৈশাখী অব্দের সূচনায় শশাঙ্কের রাজত্বের শুরুর দিকের একটি উৎসবিন্দুকে ধরে গণনা সম্ভব।
দুই
এ কথা সর্বজনবিদিত যে হরপ্পা সভ্যতার পতনের পরে তন্ত্রধর্মীয় সভ্যতার ভরকেন্দ্র পূর্ব ভারতে সরে আসে। পূর্ব মাগধী সভ্যতার ধারক ও বাহক বাঙালি জাতির অতুল কীর্তি ছিল গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্য, যা নন্দ সাম্রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন ছিল, এবং মহাপদ্মনন্দ, যিনি গঙ্গারিডাই জাতির নায়ক, তিনিই পরে মগধের রাজা হন, Curtius দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ নন্দ সাম্রাজ্য বাঙালির সৃষ্টি। আবার মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্রষ্টা শ্রীগুপ্ত বর্তমানের মালদা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মৃগস্থাপন স্তূপ থেকে এসেছিলেন আমরা জানি (আমার লেখা “বাঙালির সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাস” দ্রষ্টব্য)। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিম কালে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রচলন, এবং মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন সেযুগের পয়লা বৈশাখের সমাপতন আমাদের কাছে বঙ্গাব্দের উৎস সন্ধানে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন।
দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কের সময় গ্রহবিপ্রদের আগমন এবং জটিল সৌরনাক্ষত্রিক গণনার প্রচলনের সম্ভাবনা আছে, যে গণনা ব্যতিরেকে বঙ্গাব্দের হিসেব করা যায় না। শশাঙ্কের সময় প্রদত্ত ভূমিদানপট্টোলী যদিও গুপ্তাব্দের উল্লেখ করে, কোনও বঙ্গাব্দের উল্লেখ নেই। বলা দরকার, শশাঙ্ক গৌড়সম্রাট ছিলেন। সেযুগে বঙ্গ বললে আজকের পূর্ববঙ্গ বোঝাত। কাজেই আমাদের বাঙালি জাতির এই অব্দ শশাঙ্কের সময় বঙ্গাব্দ নামে অভিহিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। মধ্যযুগেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায় যে গৌড়ীয় শব্দটিই বাঙালির সমার্থক ছিল। তাই বঙ্গাব্দ বলে অভিহিত হওয়ার ঘটনাটি মধ্যযুগের শেষের দিকে ঘটেছে, তার আগে গৌড় বা রাঢ়ভূমিতে বঙ্গাব্দ শব্দের প্রচলন খুব একটা থাকার কথা নয়, এই বৈশাখী বছর যদিও ধর্মীয় তিথির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। অর্থাৎ এটি মূলত তন্ত্রাব্দ, উৎসবাব্দ ছিল। শাসনাব্দ নয়।
শশাঙ্কের সময় এই অব্দ প্রচলিত হলেও সেটির নাম সম্ভবত ভিন্ন ছিল, এবং সেই অব্দ শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ছিল না, স্পষ্ট করা দরকার। রাজার অভিষেক অথবা রাজ্যজয় উপলক্ষে প্রচলিত অব্দ সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শশাঙ্কের সময় বঙ্গাব্দের ব্যবহার সরকারি নথিতে দেখা যায় না। পালযুগের শেষে এবং সেনযুগের শুরুতে শকাব্দের প্রচলন হয় বাংলায়, কিন্তু সেখানেও বঙ্গাব্দের ব্যবহার নেই কোনও।
কিন্তু আকবর তত্ত্বটি মিথ্যা, আকবরের বঙ্গাব্দ প্রচলনের পক্ষে একেবারে কোনও নথি নেই, যা মোগলদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণ্য রায় বলেই গৃহীত হবেঃ বঙ্গাব্দ আকবর প্রচলন করেন নি। তারিখ ই ইলাহি ও বঙ্গাব্দ কোনওভাবে সম্পর্কিত নয়, হিজরি সন থেকে গণনা করে বঙ্গাব্দ প্রচলনের কোনও নির্দেশ আকবর দেন নি, তারিখ ই ইলাহি হিজরি সন নয়, আকবরের সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে গণনা করা হত, আকবর হিজরি সন পছন্দ করতেন না, পয়লা বৈশাখে কোনও ফসল সংগ্রহ হয় না, অতএব ফসলি সনের কথাটাও অসম্ভব। আসামে আকবরের সময় আদৌ মোগল শাসন ছিল না, কিন্তু আসামেও বঙ্গাব্দের অনুরূপ বৈশাখী নববর্ষ প্রচলিত, তারা ভাস্করাব্দ বলেন, ভাস্করবর্মার প্রচলিত বলে দাবি করেন (তাৎপর্যপূর্ণঃ কারণ শশাঙ্কের সমকালে এই ভাস্করবর্মা শাসন করতেন কামরূপ)। সূর্য সিদ্ধান্তের সময় থেকে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বৈশাখী নববর্ষের প্রচলন। সর্বোপরি আকবরের বঙ্গাব্দের পক্ষে একটিও মোগল নথি নেইঃ আকবরের বঙ্গাব্দ প্রচলন একটি অসত্য ও অর্বাচীন রটনা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই রটনাটিকে কবরস্থ করার সময় এসেছে।
তিন
বৈশাখী নববর্ষ একটি তন্ত্রধর্মীয় উৎসব। চৈত্রমাসে বাসন্তী দুর্গাপুজোর মাধ্যমে মাতৃকা উপাসনার একটি চক্র শেষ হতঃ শারদ দুর্গাপুজো থেকে বাসন্তী দুর্গাপুজো পর্যন্ত যে সময়, অর্থাৎ শরত থেকে বসন্ত, এই সময়েই বাঙালি সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করতেন, বাঙালি বণিক সমুদ্রযাত্রা করতেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে সেই যাত্রা শেষ হত, এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে উপমহাদেশের আবহাওয়া তেমন অনুকূল নয় বলে সবাই ঘরে ফিরে আসতেন। এখনও সংক্রান্তির দিনে অপ্রবাসী থাকার প্রথা আছে।
বলা দরকার, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বাংলার তন্ত্রের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যা খনার বচন থেকেও স্পষ্টঃ আমাদের চৈত্রশেষে নতুন বছর কোনও প্রশাসনিক নিয়ম নয়, বরং এর পেছনে আমাদের তন্ত্রাশ্রয়ী জীবনচর্যা ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির সময় একাধিক তন্ত্রধর্মীয় উৎসব, যেমন নীলাবতীর পুজো, চড়ক – ইত্যাদি উদযাপনের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় চক্র, কালচক্রের আবর্তন অনুষ্ঠিত হত। হরপ্পা সভ্যতার শিল্পপ্রযুক্তি দেখলে বোঝা যায় তন্ত্র ও বিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, এ প্রসঙ্গে আমার একটি প্রবন্ধ আছে (সিন্ধু থেকে সুতানুটিঃ বাঙালির জাতীয় শিল্পকর্মের ইতিহাসের একটি রূপরেখা)।
ঊষা হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকা ছিলেন, ডি ডি কোসাম্বি সিদ্ধান্ত করেছেন। আবার ঊষার শারদীয়া বোধন হত, সেই শারদীয়া বোধন থেকেই আজকের শারদীয়া দুর্গোৎসব এসেছে, এই সিদ্ধান্ত করেন সুকুমার সেন। অতএব ঊষা আদিমাতৃকার শারদীয়া বোধন হত হরপ্পা সভ্যতায়। কাজেই সৌর উৎসবের আবহ উপমহাদেশের তন্ত্রে প্রথম থেকেই আছে। আবার অন্যদিকে কালের অধিষ্ঠাত্রী কালী। তন্ত্রযানের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ হিসেবে কালচক্রযান আমরা জানি পালযুগ থেকেই জনপ্রিয়, এবং ভারতীয় সভ্যতায় কালগণনা, বর্ষগণনা অবশ্যই কালের তন্ত্রধর্মীয় ধারণায় সম্পৃক্ত। অন্যদিকে তারা উপাসনার উৎস বাঙালি জাতির মধ্যে, তারা বাংলার নিজস্ব মাতৃকা, এরকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সরকার। তারা আসলে নক্ষত্রমাতৃকা যিনি রাতের সমুদ্রে নৌকো করে পাড়ি দেওয়া বণিকদের বিপদতারণ করতেন, এমন মত আছে, এছাড়া সন্তানকোলে মাতৃকা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি। হরপ্পা সভ্যতায় নৌকোবাহিনী মাতৃকা পাওয়া গেছে, এবং সন্তানকোলে মাতৃকাও পাওয়া গেছে। চান্দ্র তিথি হিন্দুর ধর্মে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেইঃ চণ্ডী আদিতে চন্দ্রী ছিলেন, সুকুমার সেন বলছেন। অর্থাৎ সৌর ও চান্দ্র তিথি গণনার ঐতিহ্য আমাদের ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
চার
বলা দরকার, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ক্যালেন্ডারের আগে কৃষিভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতা অথবা পূর্ব ভারতে গড়ে ওঠা ব্রতধর্মীয় ব্রাত্যদের কৃষিসভ্যতায় কোনও এক ধরনের সৌর ও নাক্ষত্র কালগণনার রীতি থাকা খুবই সম্ভবঃ কারণ কৃষিকাজে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়।
অন্তিম হরপ্পা সভ্যতার পতনের পরে (২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পূর্ব ভারতে পক্ষীমাতৃকা উপাসক পাণ্ডু রাজার ঢিবির যে তন্ত্রধর্মীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে, মোটামুটি তারও পতন ঘটে যায় ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ, এরপর চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গাল সভ্যতার পতন ঘটে আজ থেকে আনুমানিক ২০০০ বছর আগে।
এই সভ্যতাগুলি তন্ত্রধর্মীয় ছিল প্রত্নসাক্ষ্য থেকে সুপ্রমাণিত, কিন্তু পতনের ফলে এদের লিপিবদ্ধ নথি হারিয়ে গেছে। ভারতে তন্ত্রের বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ নথি আসলে পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে গৌড়ের উত্থানের সময় থেকেই পাওয়া যায় (ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাম্প্রতিক তন্ত্র এনলাইটেনমেন্ট টু রেভলিউশন প্রদর্শনীর স্মারকগ্রন্থে এই পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের টাইমলাইন দেওয়া হয়েছে), এবং বৈশাখী নববর্ষের উৎসব গৌড়বঙ্গে এই সময়ে তন্ত্রধর্মের উদযাপন হিসেবে শুরু হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।
শিব ও নীলাবতীর বিবাহের উৎসব হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন, নীলষষ্ঠী। ষষ্ঠী নামেও সৌর উৎসবের আবহ আছে। একটি তন্ত্রধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে নতুন বৈশাখী বর্ষবরণ করার ঐতিহ্য গৌড়ে শশাঙ্কযুগে হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। শশাঙ্ক শৈবতান্ত্রিক ছিলেন, তাঁর মুদ্রায় এক দিকে বৃষপৃষ্ঠে শিব (অথবা বৃষপৃষ্ঠে শশাঙ্ক স্বয়ং) অন্য দিকে রাজলক্ষ্মী আছেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে শিব ও চণ্ডীর একটি উৎসব শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রথম প্রচলিত হওয়ার একটি নথিবদ্ধ প্রমাণ আছে, আমি আগে উল্লেখ করেছি “বঙ্গাব্দের উৎস” শীর্ষক প্রবন্ধে।
গুপ্তযুগে অগ্রহায়ণ নতুন বছরের প্রথম মাস ছিল। সেখান থেকে বৈশাখে নতুন বছরের সরে আসা, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের বদলে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রচলন, ও মহাবিষুবের দিনে নতুন বৈশাখী বর্ষের সূচনার পেছনে একটি চিন্তন বিপ্লব ছিল সন্দেহ নেই। বলা দরকার, আগের অগ্রহায়ণ নববর্ষটিও তন্ত্রাশ্রয়ী মাতৃকাবর্ষ ছিল, কারণ শারদীয়া বোধন থেকে কার্তিকী অমাবস্যা অবধি একটি একটানা উৎসবের আবহের পরেই নতুন বছর আসত অগ্রহায়ণে। কিন্তু সেগুলি সবই চান্দ্র তিথি মেনে আয়োজিত উৎসব, যদিও মলমাসের ধারণার মাধ্যমে সৌর ও চান্দ্র মাসের মধ্যে সাজুয্য স্থাপন হয়েছে পরবর্তীকালে। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তির (গাজন, নীলষষ্ঠী, চড়ক প্রভৃতি) উৎসবের মধ্য দিয়ে বর্ষশেষের উৎসবে চান্দ্র তিথি পুরোপুরি বর্জন করে স্থায়ী সৌর তিথির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে কৃষিনির্ভর সভ্যতার জন্য উপকারী, কারণ তা বর্ষের আবর্তনে ঋতুর সাজুয্য স্থাপন করে, ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়েই নববর্ষের আবাহন হতে লাগল।
বৈশাখের ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় মাতৃকা উপাসনার একটা ঐতিহ্য আছে, এই সময় আজও মা সিংহবাহিনী গন্ধেশ্বরীর পুজো হয়। বুদ্ধপূর্ণিমাও একই দিনে। বলা দরকার উপমহাদেশে তন্ত্রধর্মীয় মাতৃকা উপাসনার উৎসব প্রায়ই পরবর্তী ধর্মসমূহ আত্মীকরণ করেছেঃ কার্তিকী অমাবস্যায় প্রদীপ সহযোগে নিশা/কালীর উপাসনা অত্যন্ত প্রাচীন, সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতা থেকে চলে আসছে (কারণ ঊষা এবং নিশা দুজনেই পূজিত হতেন হরপ্পা সভ্যতায়, সুকুমার সেন বলছেনঃ একজন বর্তমানে দুর্গা অন্যজন কালী রূপে পূজিত হচ্ছেন), এই দিনই আবার জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের মহানির্বাণ দিবস, মহাবীরের মহানির্বাণকে স্মরণীয় করতে আলো জ্বালানো হত, আবার এই দিনেই রামায়েত বৈষ্ণব ধর্মের দিওয়ালি, রামের অযোধ্যায় ফেরার আলোকোৎসব।
পাঁচ
আকবর করেন নি, নিশ্চিত। প্রশ্ন এটাইঃ শশাঙ্ক করেছিলেন কি? শশাঙ্ক করেছেন তার তেমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে যা বলা হচ্ছে, সেই ৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম বঙ্গাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক অথবা যৌবরাজ্যে অভিষেক, অথবা রাজ্যজয় ইত্যাদির কোনও নথি নেই। শশাঙ্কের রাজত্বকালের প্রথম নথিবদ্ধ উল্লেখ আমরা সপ্তম শতকের শুরুর বছরগুলি থেকে পাই। ৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড় কর্ণসুবর্ণে মহারাজাধিরাজ রূপে রাজত্ব করছেন, নাকি শশাঙ্ক তখন রোহটাস অঞ্চলে শাসন করছেন, প্রকাণ্ডযশ জয়নাগের মহাসামন্ত হিসেবে (মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের সীল পাওয়া গেছে রোহটাসগড় থেকে) সেটা নিশ্চিত করে বলার মত নথি নেই। শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্রে বঙ্গাব্দের বৈশাখী উদযাপনের স্থান থাকতেও পারে, ছিল সম্ভবত, কারণ চৈত্রশেষের শৈব শাক্ত তন্ত্রধর্মীয় উৎসবগুলি সেদিকে ইঙ্গিত করছে, কিন্তু রাজকীয় নথি দেখে তো নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে শশাঙ্কের রাজত্বকালের নথির প্রাচুর্য নেই, অভাব আছে, সেটাও ঠিক। বাণভট্টের হর্ষচরিত আছে। আমাদের ইতিহাসে কোনও শশাঙ্কচরিত নেই।
তবে শশাঙ্কের রাজত্বের শেষের দিকেও শাকদ্বীপি প্রভাবে নতুন অব্দের প্রচলন হয়ে থাকতে পারে, এবং নতুন অব্দের প্রচলনের সময় শশাঙ্কের রাজত্বের শুরুর দিকে একটি বছরকে উৎসবিন্দু ধরে নেওয়া সম্ভব, আগেই আলোচনা করেছি এই বিষয়ে। শেষের দিকে প্রচলিত হলে শশাঙ্কের নথিতে এই নতুন অব্দের অনুল্লেখের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
শশাঙ্কের সময়ে গৌড়বঙ্গে প্রচলিত হয়ে থাকতেই পারে এই বৈশাখী বর্ষবরণ ও নতুন অব্দ, এই সিদ্ধান্তজ্যোতিষ-নির্ভর ক্যালেন্ডার, যা সেইযুগে উপমহাদেশের এক বৃহৎ অংশেই ঘটেছে। সেইযুগে পয়লা বৈশাখ মহাবিষুব সংক্রান্তির খুব কাছাকাছি ছিল (৫০০ খ্রীষ্টাব্দে যদি পয়লা বৈশাখ মহাবিষুবের দিন ২২শে মার্চ ঘটে থাকে, তবে ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তা মোটে ১.৫ দিন এগিয়ে এসে ২৩শে মার্চ হবে)। কিন্তু এই নতুন অব্দের প্রচলন ঘটে থাকলেও তা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজের জন্য যে ব্যবহৃত হয় নি, তা নিশ্চিত। এটি ধর্মীয় উৎসব ছিল, আজও সমস্ত শেকড়বিচ্ছিন্নতা ও ইতিহাসবিস্মৃতির মধ্যেও আমাদের পয়লা বৈশাখ তন্ত্রধর্মীয় উৎসবই আছে।
এবং জয়নাগবংশীয় শশাঙ্ক চৈত্রশেষে নানা উৎসবের মাধ্যমে বৈশাখী নববর্ষের উৎসবাব্দ প্রচলন করেছিলেন, নাকি জয়নাগ স্বয়ং করেছিলেন, শশাঙ্ক করে থাকলে রাজত্বের শুরুতেই করেছিলেন নাকি শেষে, এগুলি পাথুরে নথির অভাবে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও নিশ্চিত করে বলা যায়ঃ যখন সূর্যসিদ্ধান্ত এলো, যখন গৌড়ের উত্থান ঘটছে, যখন গৌড়তন্ত্র তৈরি হচ্ছে, যখন শ্রীশ্রীচণ্ডী লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যখন থেকে প্রাচীন যুগের ভারতে তন্ত্রের নথিবদ্ধ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছি আমরা, যখন থেকে বাঙালি জাতি তার শেকড় পুনরুদ্ধারের অভিযাত্রা করেছে, তখনই দক্ষিণ এশিয়ার এক বৃহৎ অংশের সঙ্গে বাংলাতেও বৈশাখী নববর্ষের সূচনা। এই নববর্ষের জনক একা শশাঙ্ক, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এক মহামন্থন থেকে উঠে এসেছিল এই বর্ষবরণ, বাঙালির ইতিহাসে গৌড়ের উত্থান এক মহাসন্ধিক্ষণ, আমার গৌড়সম্ভব দ্রষ্টব্য। গৌড়ের উত্থান ও বৈশাখী নববর্ষের আগমন একসঙ্গে ঘটেছিল।
বাঙালির ইতিহাস ছিন্নপত্র, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। এমন অবস্থায় বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাসের ইঙ্গিতকে অবহেলা করলে কালাপাহাড়ের মতই ধ্বংসাত্মক কাজ হবে, সে কাজ আমরা করব না এবং অপর কাউকে করতেও দেব না। বাঙালির ইতিহাসের ইশারা, আভাস, ইঙ্গিতগুলি আমরা তীব্রতম মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করব।
তথ্যসূত্র
- ১। M N Saha and N C Lahiri – History of the Calendar in Different Countries through the Ages। CSIR, Delhi, 1992.
- ২। সুকুমার সেন রচনাসংগ্রহ। আনন্দ, কলকাতা।
- ৩। তমাল দাশগুপ্ত – বঙ্গাব্দের উৎস (মাৎস্যন্যায় পত্রিকা)
- ৪। তমাল দাশগুপ্ত – বিস্মৃত গৌড়সম্রাট জয়নাগের স্বর্ণমুদ্রা ও ভূমিদানপট্টোলী (সপ্তডিঙা পত্রিকা)
- ৫। তমাল দাশগুপ্ত – সিন্ধু থেকে সুতানুটি (সপ্তডিঙা পত্রিকা)
- ৬। Imma Ramos – Tantra Enlightenment to Revolution. Thames and Hudson, London, 2020.























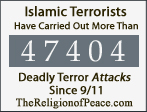




0 Comments