সহজ যোগাযোগব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট মাটির সহজলভ্যতা এবং দক্ষ মৃৎশিল্পীদের উপস্থিতির কারণেই রায়েরবাজারে গড়ে ওঠে এ পালপাড়া। রায়েরবাজারের পশ্চিম পাশ দিয়ে একসময় বয়ে যেত একটি প্রশস্ত খাল। এ খালের একটি মুখ বুড়িগঙ্গা এবং অন্য মুখটি সংযোগ রক্ষা করত তুরাগের সঙ্গে। পালদের তৈরি মৃৎপাত্র নৌকাবোঝাই হয়ে এ খাল দিয়েই ছড়িয়ে পড়ত সারা দেশে। ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ আসাদ, লিখেছেন স্বপন কুমার দাস
ঢাকার অতি প্রাচীন জনপদ রায়েরবাজারের পালপাড়া। পাল বা মৃৎশিল্পীদের বসবাসের কারণেই এ এলাকার এ নাম। তবে কাগজে-কলমে পালপাড়া বলে কোনো জায়গা এখানে নেই। পুলপাড়, জাফরাবাদ, সুলতানগঞ্জ, নিমতলী, কল্লাবাগ ইত্যাদি এলাকাজুড়ে ছিল পালদের বসবাস। তবে পুরো এলাকাটি ছিল একসময় জাফরাবাদ মৌজার অন্তর্গত। এককালে এ এলাকার অসংখ্য মৃৎশিল্পীর হাতে গড়া মৃৎপাত্রের কদর ছিল সারা দেশে।
আদিতে রায়েরবাজার পালপাড়ায় ছিল দুই শ্রেণীর পাল। এক শ্রেণীকে বলা হতো রাজবংশী পাল, অপর শ্রেণীকে বলা হতো রুদ্র পাল। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদের রাজবংশী পালরা এ এলাকায় এসে আস্তানা গাড়েন। রাজবংশী পালদের আসার আগে এখানে বাস করত রুদ্র পালরা। তারা সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র তৈরি করতেন। আর রাজবংশী পালরা তৈরি করতেন নানা দেব-দেবীর প্রতিমা। এ দুই শ্রেণীর পালদের সমন্বয়ে এখানে গড়ে উঠেছিল মৃৎশিল্পের জমজমাট এক বাজার।
সহজ যোগাযোগব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট মাটি প্রাপ্তি এবং দক্ষ মৃৎশিল্পী থাকায়ই রায়েরবাজারে পালদের বসতি গড়ে ওঠে। রায়েরবাজারের পশ্চিম পাশ দিয়ে একসময় বয়ে যেত একটি প্রশস্ত খাল। এই খালের এক অংশ বুড়িগঙ্গা এবং অপর অংশ তুরাগ নদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। পালদের তৈরি মৃৎপাত্র নৌকা বোঝাই হয়ে এ খাল দিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানে যেত। মৃৎপাত্র কিংবা প্রতিমা তৈরি করতে দুই ধরনের মাটির প্রয়োজন হয়। একটি আঠালো কালচে মাটি, অপরটি লালমাটি। বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় পাড়ে কালচে রঙের মাটি সহজে পাওয়া যেত। আর তুরাগ নদের উত্তর পাড়ে পাওয়া যেত লাল মাটি। গরুর গাড়ি ভর্তি হয়ে এ মাটি নিয়ে আসত এক শ্রেণীর মাটি ব্যবসায়ীরা। এ মাটি দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে মৃৎশিল্প পসরা সাজাতেন পালরা।
রায়েরবাজারের পালদের তৈরি মৃৎশিল্পের চাহিদা ছিল দেশজোড়া। এখানকার তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, কলস, ঘট, টালি ইত্যাদি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ছিল টেকসই। তা ছাড়া মাটির তৈরি বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিমূর্তি, দেব-দেবী, লক্ষ্মী সরা ইত্যাদির বিস্তর চাহিদা ছিল। মহাজনরা নৌকা বোঝাই করে মৃৎশিল্প সামগ্রী বয়ে নিয়ে যেত। স্থানীয় পালদের মধ্যে ছিল দুুটি সম্প্রদায়। একদল শুধু তৈরি করত। অপর দল তৈরি জিনিস মহাজনদের কাছে বিক্রি করত। বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে সহজে বেচাকেনার জন্য ১৯১৮ সালে গড়ে উঠেছিল গদিঘর। সামান্য পয়সার বিনিময়ে এই গদিঘর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করত। এই গদিঘরের কর্তারা হিন্দুদের জন্য এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। আর এখানে আগত মুসলমান ব্যবসায়ীদের নামাজের জন্য দুটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়। মন্দির এবং মসজিদগুলো আজও আছে। আছে গদিঘরের জৌলুশপূর্ণ সেই বাড়িটিও। তবে গদিঘরটি এখন বেদখল হয়ে গেছে।
এভাবেই রায়েরবাজারের পালদের বিস্তৃতি ঘটে। একসময় পাল পরিবারের সংখ্যা বেড়ে হয় সাত শতাধিক। পরিবার-পরিজন নিয়ে খেয়েদেয়ে তাদের সংসার ভালোই চলে যেত। কিন্তু এ সুখ পালদের কপালে বেশি দিন সইল না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থানের কারণে তাদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দেয়।
গত শতকের ত্রিশ ও চলি্লশের দশকে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন শুরু হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এ পাড়ায়। মুসলিম লীগের কিছু গুণ্ডা নানাভাবে নির্যাতন করে তাদের। মন ভেঙে যায় এখানকার সম্পন্ন পালদের। কেউ কেউ দেশত্যাগ করে পাকিস্তান হওয়ার পর। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রায়েরবাজারের পালদের কোমর ভেঙে যায়। সেবার মোহাম্মদপুর থেকে আসা বিহারিরা এবং হাজারীবাগের ট্যানারিতে কর্মরত নোয়াখালী অঞ্চলের শ্রমিকরা উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে পুরো পালপাড়া লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আগুন দিয়ে প্রতিটি ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সে আক্রমণে ৯৬ জন খুন হন। অসংখ্য আহত হন। বহু নারী ধর্ষিত হন, অপহরণ করেও নিয়ে যাওয়া হয় বহু তরুণী-যুবতীকে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে পালরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। মাত্র শতাধিক পাল রয়ে যান পালপাড়ায়। কয়েক বছর পর পালদের জীবনে আবার দুর্যোগ নেমে আসে। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা এবং বিহারিরা পালপাড়া আক্রমণ করে বহু লোককে হতাহত করে। ঘরবাড়িতে লুটপাট চালায়। হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া পালরা পুরো ৯ মাস এখানে-সেখানে পালিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকে। দেশ স্বাধীন হলে আবার তারা ফিরে আসে। কিন্তু আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না নানা কারণে। কেউ কেউ পেশা পরিবর্তন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এভাবে পালদের সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে পাঁচ-ছয়টি পরিবারে এসে নেমেছে। একসময় রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ দোকানগুলোতে বসত মৃৎশিল্পের পসরা। এখন সেসবের কিছুই নেই। পালপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া খালটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।
এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গুটিকয় পাল পরিবার আজও তাদের পৈতৃক পেশা আঁকড়ে আছেন। এখনো তারা বাড়ির আঙিনায় মৃৎপাত্র তৈরি করে বিক্রি করে। তাদের কারো কারো এখন দেশজোড়া খ্যাতি। এর মধ্যে মরণচাঁদ পাল অন্যতম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। পালপাড়া দিয়ে হেঁটে বেড়ালে আজও দু-একটি মৃৎশিল্পের দোকান চোখে পড়ে। শতাধিক বছরের প্রাচীন কালীমন্দির, স্থাপত্যিক সৌকর্যময় রাধা-মাধব মন্দির আর গদিঘর মনে করিয়ে দেয় এককালের রায়েরবাজারের পালদের সমৃদ্ধির কথা।
সূত্র: কালের কণ্ঠ























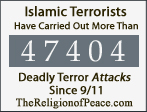




0 Comments